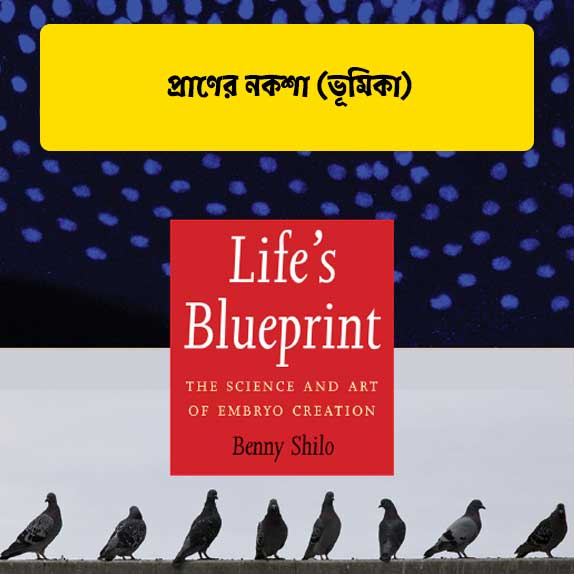
নিচের পোস্ট-টা মলিকুলার জেনেটিক্স গবেষক বেনি শিলো-র লেখা ‘Life’s Blueprint’ বইটার সূচিপত্র ও ভূমিকার অনুবাদ।
সূচিপত্র
(বাকি অধ্যায়গুলো ক্রমশ প্রকাশিত হবে….)
ভূমিকা
নিষেক বা fertilization-এর সময়, ডিম্বাণু (egg) আর শুক্রাণুর (sperm) মধ্যে থাকা জিনগত উপাদান, অর্থাৎ বাবা এবং মায়ের প্রত্যেকের জিনগত উপাদানের অর্ধেক অর্ধেক মিলিত হয়ে একটা নতুন কোষ আবির্ভূত হয়। ওই একটা কোষ থেকেই ভ্রূণের পথযাত্রা শুরু। ওই এককোষী ভ্রূণ থেকে একদিন একটা বহুকোষী জীবের সৃষ্টি হবে, তার ভয়ঙ্কর জটিল সব কলা সমেত। তার মধ্যে কোষগুলো হবে নানা প্রকারের, তারা পালন করবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। এই বৈচিত্র সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য মজুত থাকে শুরুর ওই একটা কোষের ডিএনএ-তেই, এবং হুবহু এই একই তথ্য ভ্রূণের প্রত্যেকটা নতুন কোষে চালান হতে থাকে।


আমাদের দেহের সব কোষেই হুবহু একই জিনগত তথ্য রয়েছে।
নিষেকের সময়, ডিম্বাণু (egg) আর শুক্রাণুর (sperm) নিউক্লিয়াস-এর মিলন হয়, এবং সৃষ্টি হয় ভ্রূণের প্রথম কোষ। এরপর সেই কোষের যতই বিভাজন হোক, সব উত্তরসূরিদেরই মধ্যেই এই জিনগত তথ্য চালান হবে। এই তথ্য একাই ভ্রূণের আকৃতি নির্ণয় করে। এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় হুবহু একই যমজদের দেখলে। তাদের জিনগত উপাদান প্রায় একই, তাই তাদের গড়নে এত মিল।
মানুষ অনেকদিন ধরেই বুঝতে চাইছে কোন কোন নিয়ম বা নির্দেশ মেনে এই ভ্রূণ তৈরী হয়,খুঁজে বার করতে চেয়েছে “প্রাণের নকশা” । এই চাওয়ার কারণ অনেক। প্রথমে অবশ্যই আমরা বুঝতে চাই মানুষ কিংবা অন্যান্য জীব তাদের জটিল দেহের সৃষ্টি করে কিভাবে? জিন-এ থাকা নির্দেশগুলোর থেকে কিভাবে সম্ভব হয় গোটা জীবটার গঠন নির্ণয়? কি সেই নির্দেশাবলী ? বারবার কিভাবে সেই নির্দেশ নির্ভরযোগ্যভাবে পালিত হয়? একবার এই নির্দেশগুলোর সন্ধান পেলে আমরা কি সেইসব রোগের কথাও বুঝতে পারবো যেখানে এই জিন-ভিত্তিক আয়োজনে গোলমাল হয়? আর ভবিষ্যতের কথা ভাবলে আরেকটা প্রশ্ন মাথায় আসে: আমাদের এই জানাটাকে কাজে লাগিয়ে কি কোষেদের দিয়ে এমন সব কলা (tissue) কিংবা অঙ্গ (organ) বানানো কি সম্ভব, যেগুলো গাড়ির “স্পেয়ার পার্টস”-এর মতো থাকবে, প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে?
এইসব মৌলিক প্রশ্নের পেছনে ধাওয়া করতে গেলে আরো কিছু প্রশ্নও চলে আসে। একটা কোষকে কি আগে থেকে প্রোগ্রাম করা থাকে যাতে সে একদম নির্দিষ্ট এক ধরণের কোষে পরিণত হবে, নাকি শুরুতে তার অনেকগুলো বিকল্প থাকে? থাকলে, সে কিভাবে বেছে নেয় কোন ধরণের কলা (tissue) বানাবে? প্রত্যেক প্রজাতিরই কি নিজস্ব নিয়মাবলী রয়েছে এবং নিজস্ব যুক্তি মেনে তার ভ্রূণবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলে, নাকি আলাদা আলাদা প্রজাতির মধ্যেও কিছু সর্বজনীন বিষয়বস্তু পাওয়া গেছে? গত তিনটে দশকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো বহুকোষী জীবের মধ্যে ভ্রূণবৃদ্ধি নিয়ে আমাদের ধ্যানধারণা ওলোটপালোট করে দিয়েছে। এই বই সেইসব বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর কথাই জানাবে, সাথে সাথে ভ্রূণবৃদ্ধির জগতে যে নতুন নিয়মগুলো বেরিয়ে আসছে, তার সাথেও পরিচয় করিয়ে দেবে।
ভ্রূণবৃদ্ধির বিশ্লেষণের অনেকটাই আণুবীক্ষণিক (microscopic) ছবি তুলে সেগুলো নিয়ে কাটাছেঁড়া করা। এই ধরণের ছবিতে ভ্রূণের বিভিন্ন কলা দেখানো হয় নানান ফ্লুওরোসেন্ট রঙে। কিংবা হয়তো ছবিগুলো সরাসরি স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোসকোপ (scanning electron microscope) থেকে পাওয়া। কিংবা হয়তো সেগুলো চলমান ছবি বা মুভি, যেখানে কলা কিংবা ভ্রূণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া লাইভ দেখা যায়। ছবিগুলো শুধু তথ্যে বোঝাই নয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চোখধাঁধানো সৌন্দর্য । অনেক গবেষক ওই ছবির টানেই অনেকসময় এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে নেমে পড়েন।
আমার কাছে, এই চাক্ষুষ দেখার আনন্দ একটা ব্যক্তিগত নেশার সাথে জড়িয়ে আছে। হাই স্কুল থেকেই আমার ফটোগ্রাফির শখ। কিভাবে আমরা আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে দেখি এবং দেখাই, সেই নিয়েই আমি ভাবতাম। শুরুর দিকে আমি স্থির বস্তুকেই ক্যামেরাবন্দী করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতাম। বস্তু আর তার সাথে আলোর খেলা নিয়ে মেতে থাকতাম। গত পনের বছরে আমি অনেকবার বিদেশভ্রমণ করেছি, দূর প্রাচ্যে ও ভারতেও গেছি। এর ফলে এবং হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গীটাও আরেকটু পরিণত হওয়ার ফলে, আজকাল আমি লোকজনের ছবিই বেশি তুলে থাকি। আমি দেখাতে চেষ্টা করি সেইসব সার্বজনীন ব্যাপারগুলোকে যা সবরকম জাতি কিংবা বয়েসের মানুষকেই এক সূত্রে বাঁধে। আবার তাদের পরিবেশের কারণে যেসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট দেখা যায়, সেগুলোকেও তুলে ধরি।
ভ্রূণবৃদ্ধির জগতের সাম্প্রতিক খবরের সাথে চাক্ষুষ পরিচয় করাতে আমি বিভিন্ন জীবের বৈজ্ঞানিক ছবি একত্র করেছি এখানে, যাতে ভ্রূণবৃদ্ধির মূল ধারণাগুলো পরিষ্কার হয়। ছবিগুলো আমার এবং আমার কিছু সহকর্মীদের গবেষণাগারে তোলা। প্রত্যেকটা ছবির সাথেই আমি আরেকটা করে ছবি জুড়ে দিয়েছি। এই দ্বিতীয় ছবিটা “বৃহত্তর জগতের” থেকে নেওয়া। বৈজ্ঞানিক ছবিটার সাথে তার কোনো না কোনোভাবে মিল আছে এবং আমার কাছে উপমা হিসেবে কাজ করে। আমি আশা করবো দুটো ছবি পাশাপাশি দেখলে পাঠক তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে কাজে লাগিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্বন্ধে অনেকটা বুঝতে পারবেন। একটা মজার ঘটনা হলো, cell (কোষ) কথাটা ১৬৬৫ সালে রবার্ট হুক ব্যবহার করেছিলেন বৃহত্তর জগতের সাথে তুলনা করে। নিজের তৈরী মাইক্রোস্কোপে কর্ক ওক (cork oak) গাছের ছাল দেখছিলেন তিনি। মৃত কোষের প্রাচীরের (cell wall) নিয়মিত সজ্জা দেখে ওনার মনে হলো, এগুলো তো সন্ন্যাসীদের কুঠুরি বা cell-এর মতো দেখতে । আমিও সেইরকম আশা করবো, ছবি দেখে যেন পাঠক নিজেকে বর্ধিষ্ণু ভ্রূণেরর মধ্যে একটা কোষ হিসেবে কল্পনা করতে পারে।


কোষ এবং মানবজগতের মধ্যে তুলনা করা যায়।
রবার্ট হুক সেই যে cell (কোষ) কথাটার চলন শুরু করলেন, সেই থেকে কোষকে মানবজগতের সাথে তুলনা করা হয়ে আসছে। হুক cell নামটা দিলেন কারণ মাইক্রোস্কোপে দেখে ওনার মনে হয়েছিল কোষগুলোর সজ্জা অনেকটা সন্ন্যাসীদের কুঠুরি বা cell-এর মতো। এই বইটাতে আমি কোষীয় পরিবেশের সাথে মানবজগতের অনেকগুলো মিল তুলে ধরবো। আমি আশা করবো, পাঠক তাদের পরিচিত পরিবেশের সাথে এইসব তুলনার মাধ্যমে নিজেকে একটা কোষের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। বুঝতে পারবে একটা ভ্রূণের জটিল কাঠামোর ভিতর একটা কোষ কিভাবে তার জায়গায় করে নেয় ।
এই বইটার উদ্দেশ্য ভ্রূণবৃদ্ধির জটিল পদ্ধতিটার একটা সহজ এবং বোধগম্য বর্ণনা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যটা আমাকে বাধ্য করেছে পদ্ধতিটার প্রত্যেকটা মূল ধারণা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে। জৈবিক প্রক্রিয়ার সাথে বৃহত্তর জগতের তুলনা করতে গিয়ে আমাকে প্রত্যেকটা প্রক্রিয়ার সারমর্ম নিংড়ে বার করতে হয়েছে, যাতে তার সাথে একটা মানানসই উপমা জুড়তে পারি। সর্বোপরি, যেহেতু এখানে ভ্রূণবৃদ্ধির একটা সম্পূর্ণ ছবি দেওয়ার চেষ্টা করছি, সেই ছবিতে কোন ধারণাটার কতটা গুরুত্ব, সেটাও খুঁটিয়ে দেখতে হয়েছে। বিজ্ঞানী হিসেবে আমার রোজকার কাজ হলো কোনো একটা নির্দিষ্ট জৈবিক প্রক্রিয়ার সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা। সেইখান থেকে সরে এসে গোটা ভ্রূণবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটা নিয়েই ভেবে দেখতে পেরে বেশ আনন্দ পেয়েছি, শিখেওছি অনেক।
(‘Life’s blueprint’ বইটা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ‘বিজ্ঞান’ টীম-এর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কুণাল চক্রবর্তী।)
The post প্রাণের নকশা (ভূমিকা) appeared first on বিজ্ঞান - বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম (An online Bengali Popular Science magazine).